প্রকাশিত : ১৩:৩৪
০২ অক্টোবর ২০২৫
অস্থিরতার বৃত্তে বাংলাদেশ: নির্বাচিত শাসন, জাতীয় ঐক্য নাকি সংস্কারের অপরিহার্য পথ?
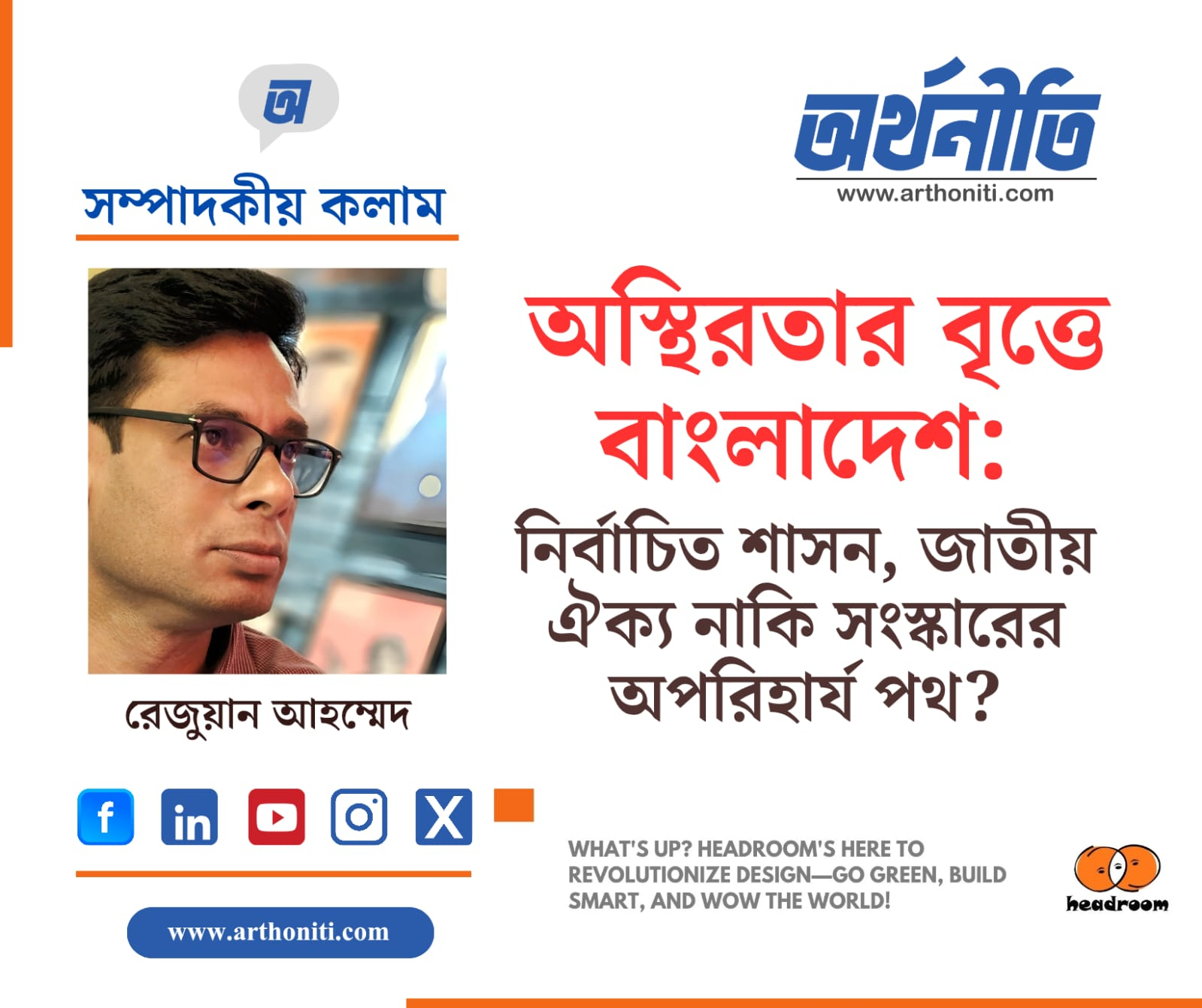
প্রশ্ন যখন অস্তিত্বের, চ্যালেঞ্জ যখন সময়ের।
অর্থনীতির ভঙ্গুর দশায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যে গভীর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে, তা কেবল ক্ষমতার পালাবদলের প্রশ্ন নয়; এটি দেশের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যমান গভীর উদ্বেগটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত; যদি দ্রুত সমস্যার সমাধান না হয়, তবে দুর্ভিক্ষের মতো বিপর্যয় আসন্ন। এই আশঙ্কার সুস্পষ্ট ভিত্তি রয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন দেশের অর্থনীতি সত্যিই ‘খাদের কিনারে’ ছিল—বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিপজ্জনকভাবে কম, মূল্যস্ফীতি তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং ব্যাংক খাত খেলাপি ঋণ ও ব্যাপক দুর্নীতির ভারে জর্জরিত ছিল। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বেকারত্বের দ্বিমুখী আঘাতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক নিম্নমুখিতা একটি গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ঝুঁকি তৈরি করেছে, যা বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ভবিষ্যদ্বাণীতেও প্রতিফলিত হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে বিতর্কটি দুটি মডেলে বিভক্ত: ১. সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে দ্রুত নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, নাকি ২. বৃহত্তর জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার মাধ্যমে গভীর কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করা। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত স্থিতিশীলতা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানো অপরিহার্য। কিন্তু সেই আস্থা নিশ্চিত করার জন্য কোনো রাজনৈতিক মডেলটি অধিক কার্যকর হবে, সেটিই এখন প্রধান প্রশ্ন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলেও, তাদের নৈতিক ভিত্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে। জনজীবনে গুণগত পরিবর্তন না আসায় এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ঘাটতি থাকায় সাধারণ মানুষের প্রাথমিক উৎসাহ কমেছে। এই নৈতিক দুর্বলতা কঠিন অর্থনৈতিক সংস্কার (যেমন: ভর্তুকি হ্রাস বা বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জ পরিবর্তন) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে। এটি স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক বৈধতা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক আস্থা ফেরানো এবং কঠিন সংস্কার বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ।
অর্থনীতির খাদ: উত্তরাধিকার, পুনরুদ্ধার ও ভঙ্গুরতা
২.১. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিপর্যয় ও প্রাথমিক পুনরুদ্ধার
বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের মূলে রয়েছে পূর্ববর্তী সরকারের দীর্ঘমেয়াদি অব্যবস্থাপনা। অভিযোগ রয়েছে যে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধিকে বাড়িয়ে দেখানো হতো। করোনা মহামারির সময় থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি মন্থর হতে শুরু করে, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক অস্থিরতায় আরও তীব্র হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৯২ শতাংশ। আগস্টের বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর তীব্র চাপ ছিল।
তবে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সামষ্টিক স্থিতিশীলতার কিছু প্রাথমিক লক্ষণ দেখা গেছে। প্রবাসীরা বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো বাড়িয়ে দেওয়ায় রিজার্ভের ওপর চাপ কমেছে, কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১০ মাস ধরে ডলার বিক্রি করেনি। ফলস্বরূপ, মে ২০২৫-এ বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৫.৪৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মানদণ্ড (বিপিএম৬) অনুযায়ী তা ২০.০৭ বিলিয়ন ডলার। মূল্যস্ফীতি এখনও উচ্চ থাকলেও (জুলাই ২০২৫: ৮.৫৫ শতাংশ), গত তিন মাস ধরে তা ধারাবাহিকভাবে কিছুটা শিথিল হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।
২.২. অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার গভীরে নীতিগত সমন্বয়ের অভাব
এই আপাত পুনরুদ্ধার অত্যন্ত ভঙ্গুর। রিজার্ভের ওপর চাপ কমা বা রেমিট্যান্স বৃদ্ধি মূলত বাহ্যিক ও সাময়িক কারণ দ্বারা চালিত, যা অর্থনীতির কাঠামোগত স্বাস্থ্যের প্রতীক নয়। ডলার বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত সাময়িক স্বস্তি দিলেও, দীর্ঘমেয়াদে বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিশীলতাকে এটি বাধাগ্রস্ত করতে পারে। অধিকন্তু, দেশের অর্থনীতি এখনও গুরুতর নিম্নমুখী ঝুঁকির সম্মুখীন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) ২০২৫ সালের জন্য বাংলাদেশের যে পাঁচটি প্রধান ঝুঁকির কথা বলেছে, তার মধ্যে রয়েছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব, অর্থনৈতিক নিম্নমুখিতা এবং চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া।
অর্থনৈতিক নীতিগত সমন্বয়ের অভাব এই ভঙ্গুরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। উদাহরণস্বরূপ, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার বাড়াচ্ছে, যা একরকম কঠোর মুদ্রানীতি। অন্যদিকে সরকার কর বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা ভোক্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং মূল্যস্ফীতিকে আরও উসকে দিতে পারে। এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, অন্তর্বর্তী সরকার সংকট ব্যবস্থাপনা শুরু করলেও, অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলো (যেমন: ব্যাংক খাতের দুর্নীতি, রাজস্ব ব্যবস্থার দুর্বলতা) কেবল কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত না হলে নতুন বিনিয়োগ হবে না, যা অর্থনৈতিক গতি ফেরানোর জন্য অপরিহার্য।
রাজনৈতিক শূন্যতা: অন্তর্বর্তী সরকারের ম্যান্ডেট ও সীমাবদ্ধতা
৩.১. উপদেষ্টাদের অভিজ্ঞতা বনাম কর্তৃত্বের সংকট
এই উদ্বেগটি অনুধাবনযোগ্য যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীতে অনভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে এই পরিষদে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নরের মতো সিনিয়র ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রয়েছেন। সমস্যাটি তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চেয়ে বরং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অভাব। অন্তর্বর্তী সরকার, যার ক্ষমতা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে গণ-অভ্যুত্থান থেকে উদ্ভূত, তাদের হাতে প্রয়োজনীয় পূর্ণ রাজনৈতিক ম্যান্ডেট বা দীর্ঘমেয়াদি সময় নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক ক্ষমতার গতি ও সীমা নির্ধারণ করে। তাদের দুর্বল নৈতিক ভিত্তি এবং রাজনৈতিক বৈধতার অভাব দীর্ঘমেয়াদি ও কঠিন সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার দিতে বাধা দেয়।
৩.২. সংস্কারের বাস্তবায়ন এবং নৈতিক ভিত্তি
অন্তর্বর্তী সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার শুরু করেছে। তারা ব্যাংক খাতে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করেছে, টাস্কফোর্স গঠন করেছে এবং ব্যাংক রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স ২০২৫ প্রণয়ন করেছে। তবে সংস্কারের সফলতা নির্ভর করবে পরিকল্পনার চেয়ে বাস্তবায়নের ওপর। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় কাঠামোগত সংস্কার (যেমন: ক্যাপাসিটি চার্জ কমানো বা ট্যারিফ কাঠামো সংশোধন) নিয়ে এখনও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই ধরনের সংস্কারে বিলম্ব পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য বড় বোঝা তৈরি করবে।
এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাথমিক নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হওয়ার প্রক্রিয়াটিও বিদ্যমান। প্রাথমিক গণ-উচ্ছ্বাস কমে যাওয়া এবং জনজীবনের গুণগত পরিবর্তন না হওয়ায় জনমনে হতাশা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে, ঐতিহাসিক দিবস বাতিলের মতো কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক দুর্বলতা এবং বৈধতার অভাবের এই চক্র দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দৃঢ় অঙ্গীকারের ঘাটতি তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত সংস্কার প্রক্রিয়াকে অকার্যকর করে দিতে পারে।
নির্বাচিত সরকারের অপরিহার্যতা ও ঝুঁকি
৪.১. সাংবিধানিক বৈধতা এবং রাজনৈতিক মূলধন
বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে জনগণের অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় সরকারের রূপরেখা এবং ৫৫ অনুচ্ছেদে মন্ত্রিসভার সংসদের কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকার বিধান রয়েছে। এই সাংবিধানিক কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নির্বাচিত সরকার অপরিহার্য।
অর্থনৈতিক সংকটের স্থায়ী সমাধানে নির্বাচিত সরকারই সর্বোত্তম ভূমিকা নিতে পারে। কাঠামোগত পরিবর্তন, যেমন: ব্যাংক খাতে বড় ধরনের সংস্কার বাস্তবায়ন এবং কঠিন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত—যেমন: ভর্তুকি প্রত্যাহার বা কর ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন—গ্রহণের জন্য একটি বৈধ ও জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার দরকার। তারা তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপরেখা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে জনগণের সম্মতি নিয়ে কঠিন পদক্ষেপ নিতে পারে। একটি নির্বাচিত সরকার দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানোর মূল চাবিকাঠি।
৪.২. সংস্কারহীন নির্বাচনের ফাঁদ
কিন্তু দ্রুত নির্বাচন হলেই দেশের মঙ্গল হবে, এমন ধারণা সরলীকৃত। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথে অতীতে দেখা গেছে, নির্বাচিত সরকারের আমলে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়নি। নির্বাচনের পর আইনের শাসন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার চর্চা সুদূরপরাহতই ছিল।
যদি নির্বাচন পূর্ববর্তী অপরিহার্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার (নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা) সম্পন্ন না হয়, তবে তাড়াহুড়ো করে একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলেও তা কেবল ‘নির্বাচনসর্বস্ব একদিনের গণতন্ত্রে’র পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। এই ফাঁদ এড়ানো জরুরি। কারণ, সংস্কারহীন নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলে তারা হয়তো অর্থনৈতিক লুটপাটের ধারা অব্যাহত রাখবে, যা বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট এবং দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিকে আরও গভীর করবে। অর্থাৎ, বৈধতা প্রয়োজন, কিন্তু সেই বৈধতা অবশ্যই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তি এবং সংস্কারের ওপর দাঁড়াতে হবে।
জাতীয় সরকারের ধারণা: ঐকমত্যের পথ ও বৈধতার চ্যালেঞ্জ
৫.১. জাতীয় সরকার এবং সংস্কারের প্রশ্ন
যেহেতু সংবিধান থেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাই ‘জাতীয় সরকার’ বলতে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বোঝানো হচ্ছে সকল প্রধান রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে গঠিত একটি দীর্ঘায়িত ট্রানজিশনাল সরকার, যার প্রধান কাজ হবে অবাধ নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রয়োজনীয় গভীর কাঠামোগত সংস্কারগুলো সম্পন্ন করা।
দীর্ঘমেয়াদি ও মৌলিক কাঠামোগত সংস্কার (যেমন: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করা এবং স্থায়ী গণতান্ত্রিক ভিত্তি তৈরি) সম্পন্ন করার জন্য একটি দীর্ঘ সময় এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন, যা স্বল্প সময়ের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি জাতীয় সরকার যদি ঐকমত্যের ভিত্তিতে দীর্ঘ সময় পায়, তবে তারা এই কঠিন সংস্কারগুলো সম্পন্ন করতে সক্ষম হতে পারে।
৫.২. সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ
জাতীয় সরকারের ধারণাটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো এর সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। ক্ষমতা বৈধকরণের জন্য এটিকে অবশ্যই জনগণের বৃহত্তর সমর্থন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে বৈধতা অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশে এই ধরনের রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা ঐতিহাসিক কারণেই অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং কঠিন।
বর্তমানে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই দ্বৈরথের বিষয়ে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি রাজনৈতিক দলগুলো প্রয়োজনীয় সংস্কার না চায়, তবে তিনি দ্রুত নির্বাচন দিয়ে দেবেন। এটি এমন এক রাজনৈতিক কৌশল, যা একদিকে দ্রুত নির্বাচনের ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলা করে, অন্যদিকে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য জাতীয় সরকার রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়াই কার্যকর থাকে, তবে এর মাধ্যমে সামরিক বা আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা বৈধকরণের ঐতিহাসিক নজিরের পুনরাবৃত্তি হতে পারে, যা গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার জন্য বিপজ্জনক।
সংস্কারের গভীরতা: অকার্যকর খাতগুলো পুনরুদ্ধার
অর্থনৈতিক সমস্যার দ্রুত সমাধান এবং দুর্ভিক্ষ বা মানবিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করার জন্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক মডেল পরিবর্তন করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন কাঠামোগত সংস্কারের বাস্তবায়ন।
৬.১. ব্যাংক খাত সংস্কার: রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরীক্ষা
বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল দুর্বলতা ছিল খেলাপি ঋণ ও দুর্নীতির ভারে জর্জরিত ব্যাংক খাত। সরকার এই খাতে কিছু উদ্যোগ নিলেও, যেমন: টাস্কফোর্স গঠন, পর্ষদ পুনর্গঠন এবং দুর্বল ব্যাংকগুলোকে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা, সফলতা নির্ভর করছে বাস্তবায়নের ওপর। ব্যাংক খাতে সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকার অপরিহার্য। কারণ খেলাপি ঋণ ইস্যুটি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি দুর্বল অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে এই রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল খেলাপী ঋণ উদ্ধার ও প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হতে পারে।
৬.২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সংস্কারের অপরিহার্যতা
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সংকট অর্থনীতির আরও একটি বড় বোঝা। বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জ কমানোর কাঠামোগত সংস্কার এবং ভর্তুকি কমানোর মতো কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরি। যদি এই সংস্কারগুলো শুরু না হয়, তবে এটি পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য আরও বড় চাপ তৈরি করবে। গ্যাস সংকটের কারণে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চালানো যাচ্ছে না, যা সরাসরি শিল্প ও বাণিজ্যে স্থবিরতা তৈরি করছে। জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম স্থিতিশীল রাখা অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ; ট্যারিফ কাঠামো সংশোধন করে যদি ভর্তুকি কমানো হয়, তবে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে, যা সামাজিক অস্থিরতার ঝুঁকি তৈরি করবে।
৬.৩. সুশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ
রাজস্ব ব্যবস্থার দুর্বলতা সরাসরি সরকারি ব্যয়, ঘাটতি অর্থায়ন এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব ফেলে। রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) সংস্কার করা প্রয়োজন। করদাতা ও কর্মকর্তাদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের পথ বন্ধ করতে হলে অনলাইন ও অটোমেশনের ব্যবহার জরুরি। সুশাসনের এই মৌলিক সংস্কার ব্যতীত, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অসম্ভব এবং দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি সর্বদা বিদ্যমান থাকবে।
মঙ্গলময় ভবিষ্যতের জন্য সুচিন্তিত পদক্ষেপ
বাংলাদেশের মঙ্গল কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মডেলের মধ্যে নিহিত নয়; বরং এটি একটি সুচিন্তিত প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। তাত্ত্বিকভাবে, গভীর কাঠামোগত সংস্কার ও গণতান্ত্রিক ভিত্তি তৈরির জন্য একটি ঐকমত্যভিত্তিক জাতীয় সরকার সময় দিতে পারত। কিন্তু এর সাংবিধানিক বৈধতার অভাব এবং রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার অসম্ভবতা এই মডেলকে অবাস্তব করে তুলেছে। অন্যদিকে, একটি নির্বাচিত সরকার সাংবিধানিক বৈধতা ও রাজনৈতিক মূলধন প্রদান করে, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে জরুরি।
সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত: দ্রুত, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পটভূমিতে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক বৈধতা পুনরুদ্ধার করা। এই নির্বাচন অবশ্যই নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগের মতো প্রতিষ্ঠানকে নিরপেক্ষ করার প্রক্রিয়া শুরু করার পর অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত তাদের সীমিত বৈধতার মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব ব্যাংক ও রাজস্ব খাতের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সংস্কারের বাস্তবায়ন শুরু করা। একই সঙ্গে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মতো কঠিন খাতে কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি করতে হবে। দেশের অর্থনীতি ও জনগণের জীবন রক্ষার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অবশ্যই দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে অর্থনৈতিক সংস্কারের সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরা এবং জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আসন্ন অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।
