প্রকাশিত : ০৮:৪০
০২ অক্টোবর ২০২৫
সোনার বাংলা: স্বপ্ন, সংকট এবং রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা
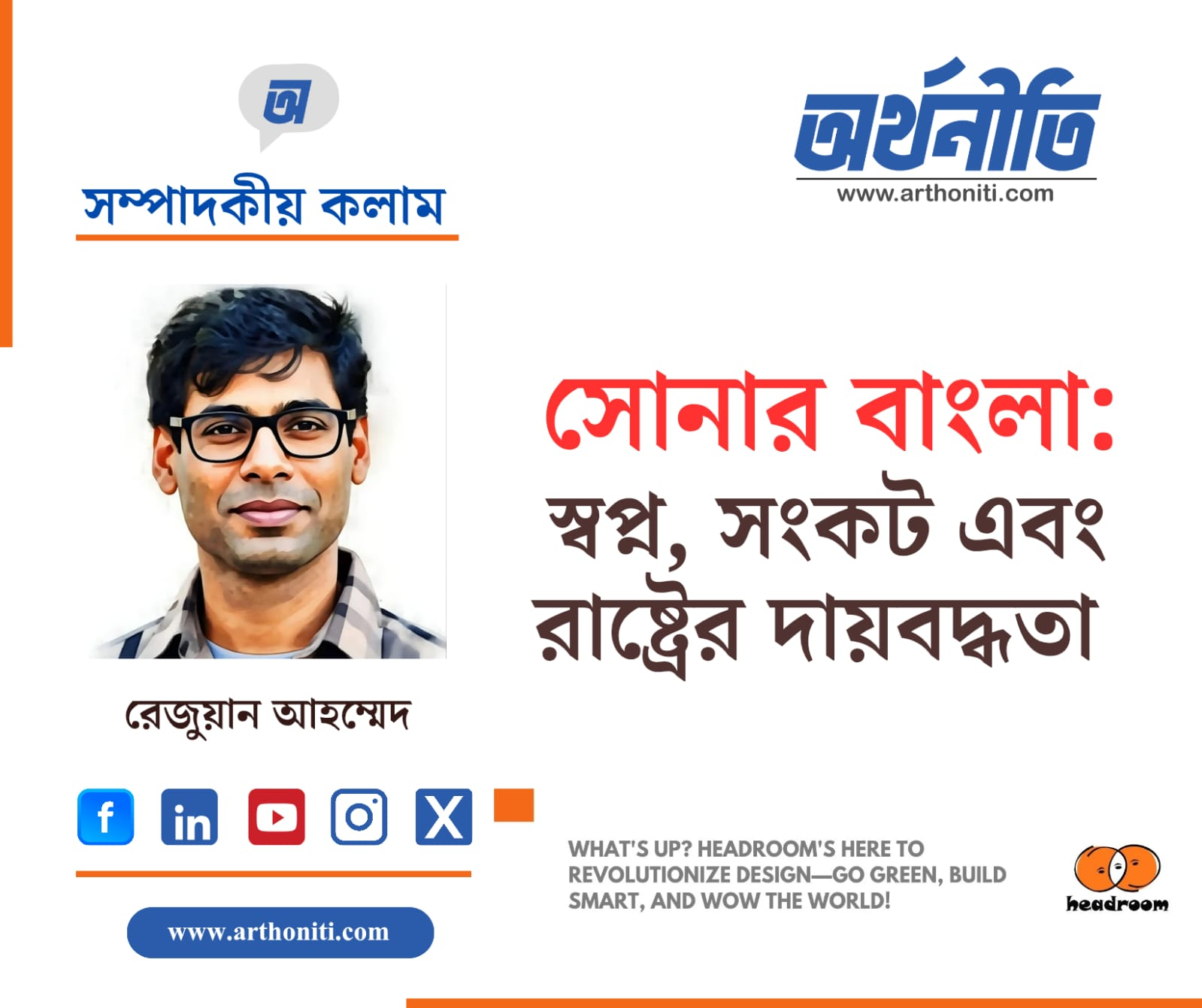
✍️ রেজুয়ান আহম্মেদ
‘সোনার বাংলা’র বিবর্ণ প্রতিচ্ছবি এবং আত্মহত্যার প্রশ্ন
বহুকাল ধরে আমরা একটি জাতীয় আকাঙ্ক্ষা লালন করে আসছি—আমাদের সেই ‘সোনার বাংলা’। এই প্রত্যয় কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি নয়; এটি মানুষের মৌলিক চাহিদা ও মানবিক মর্যাদার নিশ্চয়তার একটি দর্শন। কিন্তু যখন সংবাদপত্রের পাতা খুললেই চোখে পড়ে অভাবের তাড়নায় বা ঋণের অসহনীয় ভারে একটি পুরো পরিবারের সম্মিলিত আত্মহত্যার মর্মান্তিক খবর, তখন প্রশ্ন জাগে: আমরা কি সত্যিই সেই স্বপ্নের পথে হাঁটছি? এই নির্মম বাস্তবতা জাতীয় আদর্শের সঙ্গে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের এক ভয়াবহ ব্যবধানকে তুলে ধরে।
এই প্রশ্নটি কেবল ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন নয়; এটি রাষ্ট্রের মৌলিক দায়বদ্ধতা পূরণের ব্যর্থতার প্রশ্ন। বাংলাদেশের সংবিধান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে,
“রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাতে নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।”
দারিদ্র্য বা ঋণের চাপে মানুষ যখন এমন চরম পরিণতি বেছে নিতে বাধ্য হয়, তখন তা রাষ্ট্রের সেই মৌলিক সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকেই নির্দেশ করে। এই পরিস্থিতি কেবল অর্থনৈতিক সংকট নয়; এটি সুশাসন এবং নৈতিকতার গভীর সংকট।
সামাজিক ট্র্যাজেডির বিশ্লেষণ
আত্মহত্যা বাংলাদেশে অপ্রাকৃত মৃত্যুর এক দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যার কারণে যেসব লোকের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী রয়েছে। এই মৃত্যুগুলো কেবল পরিসংখ্যান নয়, বরং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যকারিতার ফাঁকফোকরও।
সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট বাজেটের ১৭.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপি’র ৩.১১ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, যার পরিমাণ ছিল ১,০৭,৬১৪ কোটি টাকা। সরকারের দাবি, তারা জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি (যেমন বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচি) বাস্তবায়ন করছে।
কিন্তু এত বিপুল বরাদ্দ এবং নীতির কার্যকারিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন থেকেই যায়। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, ঋণের বোঝা এবং ব্যবসায়িক মন্দার মতো সামষ্টিক অর্থনৈতিক ধাক্কা যখন প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষকে আঘাত করে, তখন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বেষ্টনী কার্যকরভাবে সেই চাপ সামলাতে ব্যর্থ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হানের মতে, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে নতুন করে দরিদ্র হওয়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কোনো বরাদ্দ নেই, এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ, কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট নতুন অর্থনৈতিক চাপগুলো সরাসরি দুর্বল জনগোষ্ঠীকে ঋণের ফাঁদে ফেলে দিচ্ছে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে পারিবারিক আত্মহত্যা। এটি প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের নীতিগত দুর্বলতা এবং সুরক্ষার অভাবই সামাজিক মৃত্যুর মূল কারণ।
অর্থনৈতিক নাজুকতা: সামষ্টিক সূচকের সংকট ও আইএমএফের প্রেসক্রিপশন
বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে খুবই নাজুক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই নাজুকতার মূল কারণগুলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর দুর্বলতা এবং নীতিগত সমন্বয়হীনতার মধ্যে নিহিত।
‘নাজুক’ অর্থনীতির মূল চালকসমূহ
অর্থনীতির প্রধান দুর্বলতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ এবং টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী দেশের মোট (গ্রস) রিজার্ভের পরিমাণ ২৫.৪৪ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি, তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর ব্যালেন্স অব পেমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম৬) অনুসারে প্রকৃত রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২০.০৭ বিলিয়ন ডলারে। রিজার্ভের এই নিম্নগামী প্রবণতা ডলার সংকটকে আরও প্রকট করেছে, যা আমদানি সক্ষমতার ওপর গুরুতর চাপ সৃষ্টি করছে।
ডলার সংকট সামাল দিতে এবং বাজেট সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হার্ড লোনের ওপর নির্ভরতা বহুগুণ বাড়িয়েছে। ২০২০ অর্থবছরে বাজেট সহায়তার প্রবাহ ছিল ১ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২২ সালে ২.৫৯ বিলিয়ন ডলারে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেকর্ড ৩.৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এসব হার্ড লোনের (যেমন এআইআইবি থেকে নেওয়া ঋণ) সুদহার বাজারভিত্তিক এবং ৬ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সুদের চাপ অন্যান্য আন্তর্জাতিক উৎসের তুলনায় বেশি হওয়ায়, ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নিয়ে শঙ্কা থাকছে। অর্থাৎ, স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক ত্রাণ পেতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ সুদের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করে তুলবে।
মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও মূল্যস্ফীতির দ্বিমুখী আঘাত
দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন একটি বহুল ব্যবহৃত নীতিগত পদক্ষেপ, যা সাধারণত আইএমএফ-এর পরামর্শে বাংলাদেশ ব্যাংক নেয়। এই সিদ্ধান্তের পিছনে প্রধান যুক্তি থাকে রপ্তানি বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক শক্তি বাড়ানো। তবে অর্থনীতিতে এই পদক্ষেপের প্রভাব মার্শাল-লার্নার শর্তের ওপর নির্ভর করে।
মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে বিদেশে পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় রপ্তানি আয় বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু একই সঙ্গে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়ে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ঘটনা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে ব্যয়-চালিত (cost-push) এবং চাহিদা-চালিত (demand-pull) দু’দিক থেকেই মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা তৈরি করে। যখন আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়ে যায় (ডলারের উচ্চমূল্যের কারণে), তখন উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পায়, যা ব্যয়-চালিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। এই মুদ্রাস্ফীতি সরাসরি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে হ্রাস করে, যা তাদের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা কঠিন করে তোলে।
আন্তর্জাতিক চাপের মুখে নীতি সংস্কারের প্রতিক্রিয়া
অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসেবে সরকারকে বেশ কিছু কঠোর নীতি ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। আইএমএফের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশ বাজেট ঘাটতি এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত পরিমাণগত পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়ার শর্তগুলো অর্জন করেছে। তবে আইএমএফের এসব কঠোর নীতির ফলে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধীর হয়ে গেছে। সংস্থাটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৪.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩.৮ শতাংশে নামিয়েছে।
কঠোর নীতিগুলোর বাস্তবায়ন এক ধরনের ‘চিকিৎসা জনিত রোগ’ (Iatrogenic Disease) সৃষ্টি করছে। একদিকে সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হচ্ছে; অন্যদিকে কঠোর নীতির কারণে বিনিয়োগ এবং বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংকুচিত হচ্ছে, যা সরাসরি সাধারণ ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে, স্থিতিশীলতা আনার প্রচেষ্টা নিজেই নতুন অর্থনৈতিক সংকট এবং অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।
রাষ্ট্র পরিচালনায় ‘আরএনডি’ মডেল: সমন্বয়হীনতা ও নেতৃত্বের সংকট
রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ মানুষের প্রয়োজন, অনভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনায় ‘আরএনডি’ (Research and Development-এর রূপক অর্থ: পরীক্ষামূলক) মডেল প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা নীতি-নির্ধারণে ধারাবাহিকতা, দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অভাবকে নির্দেশ করে। কার্যকর নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বর্তমান নীতি কাঠামোর দুর্বলতা সমন্বিত পদ্ধতির অভাবকে প্রমাণ করছে।
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সঙ্গে সরকারের অন্যান্য নীতিগুলোর সমন্বয়। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের মতে, এই সমন্বয় বর্তমান বাজেটে অনুপস্থিত ছিল। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাজস্বনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, তখন নীতিগুলো কেবল তাৎক্ষণিক সংকট সামাল দিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার মতো মনে হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে।
এই সমন্বয়হীনতা এবং দুর্বলতা ব্যাংকিং খাতসহ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিকে আঘাত করছে। কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় সরকারের ব্যয়ের সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এছাড়া, সৎ করদাতাদের করের টাকা দুর্নীতিমুক্ত খাতে ব্যবহার হচ্ছে কি না, তার নিশ্চয়তাও নেই, যা জনসাধারণের আস্থা কমায়।
ব্যাংকিং খাতের বিপর্যয়: কাঠামোগত দুর্বলতার উৎস
ব্যাংকিং খাত অর্থনীতির প্রাণ। দেশের আর্থিক খাত খুব বড় না হওয়ায় প্রায় ৯০ শতাংশ অর্থই ব্যাংক খাত থেকে আসে। স্বাধীনতার পর দেশের উদ্যোক্তাশ্রেণি গঠনে এই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই খাত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়েছে, যা বর্তমানে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।
খেলাপি ঋণের বিশাল উল্লম্ফন ব্যাংকিং খাতের এই দুর্বলতার প্রধান প্রতীক। ২০০৮ সালে যেখানে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা, ২০২৪ সালের জুনে তা বেড়ে ২ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। খেলাপি ঋণের এই বিশাল পরিমাণ এবং মূলধনের অপ্রতুলতা (বিশেষ করে ১০-১২টি ব্যাংকের ক্ষেত্রে) ব্যাংকগুলোকে দুর্বল করে দিচ্ছে। যখন ঋণ আদায় হয় না, তখন ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে ভোগে এবং সীমিত পুঁজির সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণপ্রবাহ কঠিন হয়ে যায়। এর ফলে সুদহারও বৃদ্ধি পায়।
এই সংকটের মূল কারণ কাঠামোগত। প্রথমত, ব্যাংকিং খাতের নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকর করা হয় না। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার অভাব। আইনি স্বাধীনতা থাকলেও বাস্তবে রাজনৈতিক কারণে সেই স্বাধীনতা প্রয়োগ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হয় না। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মতে, ব্যাংকিং খাত সংস্কারে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজে-কলমে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করলেও বাস্তবায়নে নেতৃত্বগত দুর্বলতা রয়ে গেছে।
বর্তমানে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করা বা সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি গঠনের মতো স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে, যা একপ্রকার ‘অগ্নিনির্বাপণ’ ব্যবস্থা। কিন্তু এসব সংস্কারের সফলতা নির্ভর করবে বাস্তবায়নের ওপর, যা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকার ছাড়া সম্ভব নয়। এই অঙ্গীকারের অভাবই প্রমাণ করে যে শাসনকার্য একটি ‘পরীক্ষামূলক’ বা ‘আরএনডি’ পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সদিচ্ছা অনুপস্থিত।
সাধারণ ব্যবসায়ীদের সংকট: অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তির বিপর্যয়
অর্থনৈতিক সংকটের সবচেয়ে সরাসরি শিকার হচ্ছেন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উদ্যোক্তারা। এই খাত একটি দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। বিশ্বব্যাপী এটি ৯০ শতাংশ ব্যবসা গঠন করে এবং ৫০ শতাংশের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। সরকার জিডিপিতে এসএমই’র অবদান ৩৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। অথচ বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বরাবরই নানামুখী সমস্যায় ভুগছে।
এসএমই খাতের ওপর দ্বিমুখী আঘাত
গত কিছুদিন ধরেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উদ্যোক্তারা বড় ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। সামষ্টিক অর্থনীতির দুর্বলতা (ডলার সংকট, উচ্চ ঋণ নির্ভরতা) সরাসরি এই খাতকে আঘাত করছে। ডলারের উচ্চমূল্য, ক্রমবর্ধমান সুদহার এবং মূল্যস্ফীতির কারণে পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া—এই ত্রিমুখী চাপে স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়ীদের টিকে থাকাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। উৎপাদন সূচকের ক্রমাগত পতনও সরাসরি এই উদ্যোক্তাদের আঘাত করছে।
এসএমই উদ্যোক্তাদের আয় ও সঞ্চয় সীমিত এবং ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতাও কম। যখন ব্যাংকিং খাতে দুর্বৃত্তায়ন এবং খেলাপি ঋণের কারণে ঋণপ্রবাহ সংকুচিত হয়, তখন সীমিত পুঁজির এই ব্যবসায়ীরা উচ্চ সুদে বেসরকারি উৎস থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হন। ফলে আমদানিকৃত কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি (মুদ্রাস্ফীতির কারণে) এবং ঋণের উচ্চ খরচ তাদের লাভের মার্জিনকে শূন্যে নামিয়ে আনে।
ঋণজালে আটকে পড়া এবং রাষ্ট্রের দায়
সামষ্টিক অর্থনৈতিক ধাক্কা যখন নীতি সমন্বয়হীনতা ও ব্যাংকিং খাতের দুর্বৃত্তায়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারাই যাদের অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা সবচেয়ে কম। এই ব্যবসায়িক ক্ষতির দায়ভার রাষ্ট্রকে অবশ্যই নিতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রীয় নীতির ভুল পদক্ষেপ বা কার্যকর নজরদারির অভাবের ফলস্বরূপ সৎ ও পরিশ্রমী উদ্যোক্তাদের পুঁজি ধ্বংস হচ্ছে।
যখন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা চলমান অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলাতে ব্যর্থ হন, তখন তাদের সীমিত পুঁজি শেষ হয়ে যায় এবং ঋণের দায় ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই চরম অর্থনৈতিক চাপ এবং হতাশা থেকেই পরিবারগুলো আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই সামাজিক ট্র্যাজেডি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ধাক্কা থেকে তার সবচেয়ে দুর্বল অথচ গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তিকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও পুঁজি গঠনে সহায়তা করা, কিন্তু বাস্তবায়নে ঘাটতির কারণে সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি।
দায়বদ্ধতা ও কাঠামোগত সংস্কারের পথে
যে দেশে অভাবের তাড়নায় মানুষকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়, সেখানে রাষ্ট্রের প্রধানের লজ্জা থাকা উচিত। এই বক্তব্য কেবল আবেগপূর্ণ নয়; এটি একটি গভীর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করে। এই ব্যর্থতা নিহিত রয়েছে টেকসই কাঠামোগত সংস্কারের অনুপস্থিতি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে।
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পুনর্মূল্যায়ন
দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করলেও, কার্যক্রমের ডিজাইন এবং বাস্তবায়নে বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। অধ্যাপক সেলিম রায়হানের মতে, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়নি এবং দুর্বৃত্তায়নের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করার উল্লেখযোগ্য দিকনির্দেশনাও নেই।
কার্যকরভাবে এই সুরক্ষা বেষ্টনী বাস্তবায়ন করতে হলে স্থানীয় সামাজিক উদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে এবং এর সুবিধা প্রকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে হবে। কেবল নগদ অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে নয়, বরং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যকে টেকসইভাবে নির্মূল করতে হবে।
অভিজ্ঞ নেতৃত্ব এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের অপরিহার্যতা
অর্থনৈতিক খাতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্র পরিচালনার ‘আরএনডি’ মডেল বন্ধ করতে হবে। শুধু স্বল্পমেয়াদী অগ্নিনির্বাপণ পদক্ষেপ নয়; প্রয়োজন সুচিন্তিত, অভিজ্ঞ এবং সমন্বিত কাঠামোগত সংস্কার।
১. ব্যাংকিং খাতের সংস্কার: রাজনৈতিক অঙ্গীকার অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনি স্বাধীনতা বাস্তবে প্রয়োগ হতে হবে। খেলাপি ঋণের লাগাম টেনে ধরে এবং ঋণ আদায় নিশ্চিত করে ব্যাংকিং সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।
২. নীতি সমন্বয়: মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। রাজস্ব আদায় বাড়াতে এনবিআরকে ডিজিটালাইজেশন এবং কর আহরণে বড় ধরনের সংস্কার আনতে হবে। রাজস্ব বোর্ডকে রাজনৈতিক সুরক্ষা দিতে হবে যাতে প্রভাবশালীরা কর ফাঁকি দিতে না পারে।
৩. এসএমই সুরক্ষা: ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা দিতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ডলারের বাজারকে স্থিতিশীল রাখা এবং উচ্চ সুদের হার কমিয়ে আনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পুঁজি এবং ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
‘সোনার বাংলা’ কেবল উচ্চ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বা ক্রমবর্ধমান জিডিপির প্রতিচ্ছবি নয়। এর মূল ভিত্তি হলো মানবিক মর্যাদা, ন্যায়ানুগ সমাজ এবং শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা সংবিধানের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদেও নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নীতিগত ‘আরএনডি’ বন্ধ করে, অভিজ্ঞ, সৎ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছাসম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমে টেকসই, ন্যায়ভিত্তিক এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বস্তুগত মানের উন্নতিসাধন নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রকে সেই সাধারণ ব্যবসায়ীদের ক্ষতির দায় নিতে হবে, যাদের ত্যাগের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় অর্থনীতির চাকা ঘোরে।
