প্রকাশিত : ১৯:২৬
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সর্বশেষ আপডেট: ২১:০৫
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অদৃশ্য লেনদেন!
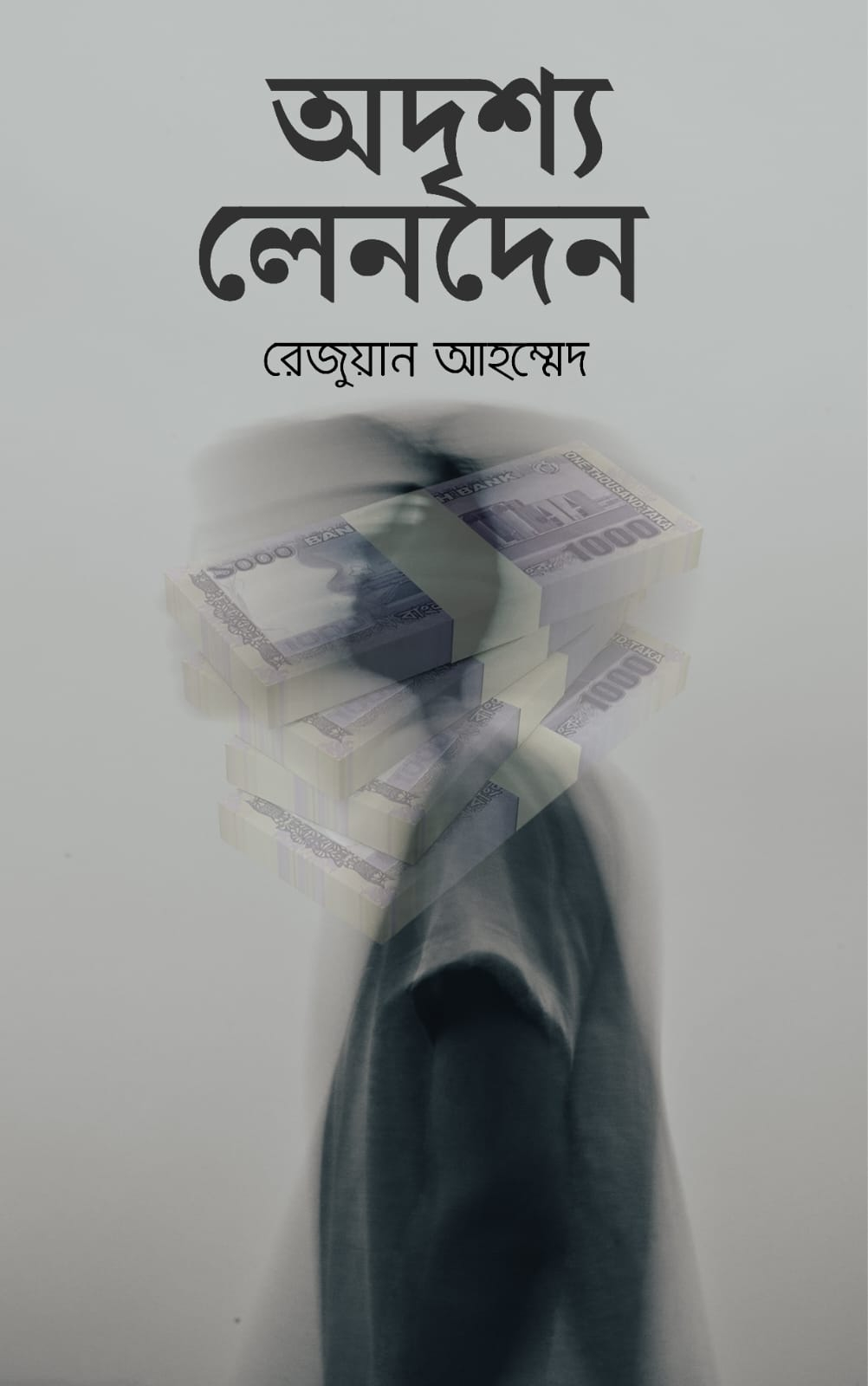
✍️ রেজুয়ান আহম্মেদ
নীতির প্রতিশ্রুতির শহরে হাবিবুর রহমান সাহেব একজন নীতিপরায়ণ মানুষ। তার বিশ্বাস, একটি রাষ্ট্র তার লিখিত নিয়মাবলী মেনে চলে, ঠিক যেমন নদী তার নিজস্ব খাত ধরে প্রবাহিত হয়। বহু বছর ধরে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার চেষ্টা তার এই বিশ্বাসের ওপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি জানতেন, কাজটি সময়সাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু নিয়মের পথে থাকলে একদিন ঠিকই হবে। তাই শহরের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা দালালদের জটলাকে তিনি ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছেন। তার কাছে সেটি ছিল অপ্রয়োজনীয় ও নীতিবিরুদ্ধ এক জঞ্জাল।
অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি সাইনবোর্ডের লেখা পড়লেন—‘ডিজিটাল বাংলাদেশ, জনগণের সেবায় নিবেদিত’। মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। পশ্চিমা তাত্ত্বিক মিশেল ফুকোর একটি উক্তি তার মনে পড়ল—‘দৃশ্যমানতাই একটি ফাঁদ’। বাইরের এই পরিপাটি, চকচকে পরিবেশ যেন এক সুপরিকল্পিত মঞ্চের মতো। চারদিকে কাচের স্বচ্ছ দেয়াল, উজ্জ্বল আলো, এমনকি কর্মচারীদের পোশাকও পরিচ্ছন্ন। এই দৃশ্যমানতা যেন জনগণকে বোঝাতে চায়, এখানে সবকিছু নিয়ম মেনে চলছে; আর এটাই সেই ফাঁদ, যা মানুষের মনে মিথ্যা আস্থা তৈরি করে। কিন্তু এই পরিপাটি আবরণের আড়ালেই যে এক অন্ধকার, অদৃশ্য লেনদেনের বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে, তা তিনি তখনো বুঝতে পারেননি।
ভেতরে প্রবেশ করে তিনি লাইনে দাঁড়ালেন, হাতে গোছানো আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফাইল। তার সমস্ত সত্তা তখন এক সুশৃঙ্খল নাগরিকের আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল। কিন্তু সেই আত্মতৃপ্তি নিমিষেই ধুলিসাৎ হলো, যখন কর্মচারী ওয়াদুদ, যিনি লাইসেন্সধারীদের ছবি তোলার কাজেও নিয়োজিত, তার ফাইলটি হাতে নিলেন। কোনো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই তিনি বললেন, “স্যার, ফর্মে ভুল আছে। রিজেক্ট।” হাবিবুর সাহেব হতাশ হলেন। কী ভুল আছে তা জানতে চাইলেও ওয়াদুদ কোনো স্পষ্ট উত্তর দিলেন না; কেবল কৌশলে এমন এক ইঙ্গিত দিলেন যা কোনো সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অংশ নয়। এই অব্যক্ত প্রত্যাখ্যান যেন তাকে সরকারি অফিসের অদৃশ্য ব্যবস্থার প্রথম ধাক্কা দিল। তার নীতির কঙ্কালসার ভিত্তি তখন কাঁপতে শুরু করল।
ওয়াদুদের নীরব প্রত্যাখ্যানের পর হাবিবুর সাহেবের নীতির সুউচ্চ প্রাসাদটি যেন একটু-একটু করে হেলে পড়ল। হতাশ হয়ে তিনি যখন অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন দালাল আতিক তার দিকে এগিয়ে এলো। নিজেকে ওয়াদুদের ‘নিকটতম বড় ভাই’ দাবি করে সে হাবিবুর সাহেবকে আশ্বাস দিল—লাইসেন্স পেতে কোনো ঝামেলা হবে না। আতিকের কথায় কোনো অপরাধবোধ ছিল না; বরং ছিল এক ধরনের পেশাদারিত্ব ও প্রজ্ঞা। সে যেন এই অদৃশ্য জগতের একজন অভিজ্ঞ মাঝি, যে নিয়মের চোরাবালি এড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ চেনে। সে হাবিবুর সাহেবকে জানাল, অফিসের প্রতিটি ইঞ্চি তার চেনা, প্রতিটি নিয়ম তার নখদর্পণে। ভেতরের অদৃশ্য প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলী সবকিছু সে জানে। তার প্রতিটি কথায় ফুটে উঠল এক গভীর বাস্তবতাবোধ, যা হাবিবুর সাহেবের এতদিনের বিশ্বাসের ঠিক উল্টো পিঠে অবস্থিত।
আতিকের মুখ থেকেই তিনি জানতে পারলেন, সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং অন্যান্য সংস্থার জরিপ অনুযায়ী বিআরটিএ-তে সেবা নিতে আসা নাগরিকদের ৬৩.২৯ শতাংশই ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছেন। আতিক বলল, “এটাই আমাদের সাফল্যের স্বীকৃতি। আমরাই সরকারি সেবায় ঘুষের শীর্ষে, যা প্রমাণ করে আমাদের দক্ষতা ও কাজের গতি।” তার এই উক্তি যেন সরকারি দুর্নীতিকে একটি শিল্প এবং সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে উপস্থাপন করল। আতিক ব্যাখ্যা করল, “অফিস চলে অদৃশ্য মূল্যতালিকা মেনে। পেশাদার লাইসেন্সের জন্য সরকারি ফি ছাড়াও দিতে হয় ২,২০০ টাকা ঘুষ। নিরক্ষর হলে খরচ আরও ৩০০ টাকা বেশি। এটা শুধু ঘুষ নয়, স্যার, বরং এক ধরনের ‘এক্সপ্রেস সার্ভিস চার্জ’। টাকা না দিলে ফাইল কেউ ছুঁয়েও দেখে না।” এই লেনদেন যেন কোনো গোপন অপরাধ নয়, বরং এক উন্মুক্ত কর্মযজ্ঞ, যা আধুনিক রাষ্ট্রের অদৃশ্য ভিত্তি।
হাবিবুর সাহেব তখন বুঝতে পারলেন, এই ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি আসলে কী। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য যে অফিসিয়াল প্রক্রিয়া—লিখিত, মৌখিক ও ফিল্ড টেস্ট—তা আসলে কোনো স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নয়; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা এক জটিল ও দীর্ঘসূত্রিতার চক্র। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ছয় মাস থেকে এক বছর সময় লাগে। এই দীর্ঘসূত্রিতাই মূলত ঘুষের চাহিদা তৈরি করে। সরকার যখন নতুন ডিজিটাল সিস্টেমের কথা বলে, তখন তা বাস্তবে কার্যকর হয় না। আতিকের মতো দালাল চক্র ও বিআরটিএ-এর অসাধু কর্মচারীরা এই সিস্টেমের দুর্বলতা ব্যবহার করে দ্রুত কাজ করার প্রলোভন দেখায়। বিআরটিএ চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার টিআইবি-এর প্রতিবেদনকে ‘অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে দাবি করে বলেন, এখন অনেক কাজ অনলাইনে করা যায়। কিন্তু হাবিবুর সাহেবের মতো মানুষেরা সেই অনলাইন প্রক্রিয়ায় কোনো সুফল পান না। অফিসিয়াল এবং দালাল-নিয়ন্ত্রিত দুটি ভিন্ন ব্যবস্থা পাশাপাশি চলে, যেখানে অফিসিয়াল ব্যবস্থাটি শুধুমাত্র ফাঁপা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এটি যেন একটি পরিকল্পিত কৌশল, যেখানে রাষ্ট্র নিজেই সেবাগ্রহীতাকে অদৃশ্য দেয়ালের দিকে ঠেলে দেয়, আর সেই দেয়াল পার হওয়ার একমাত্র পথ হলো ঘুষ নামক অনানুষ্ঠানিক লেনদেন।
ড্রাইভিং লাইসেন্সের কাজ শেষ করে হাবিবুর সাহেব এবার গেলেন পাসপোর্ট অফিসে। তার পাসপোর্টের নামের বানানে একটি ছোট ভুল, যা সংশোধন জরুরি। কিন্তু এখানে এসে তিনি দেখলেন ভিন্ন চিত্র। এখানে ঘুষ কেবল একজন বা দুজন দালালের হাতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং একটি ‘গণতান্ত্রিক’ ব্যবস্থার মতো পুরো অফিসজুড়ে ছড়িয়ে আছে। দারোয়ান থেকে আনসার, সহকারী পরিচালক—সকলেই যেন সিন্ডিকেটের অংশ। ঘুষ নেওয়া এখানে অপরাধ নয়, বরং সবার অংশগ্রহণে এক সম্মিলিত উৎসব। হাবিবুর সাহেব দেখলেন, এই অফিসে ক্ষমতার স্তরবিন্যাস পদমর্যাদার ওপর নির্ভর করে না; বরং এই অদৃশ্য ঘুষব্যবস্থায় কার অবস্থান কতটা শক্তিশালী, তার ওপর নির্ভর করে। একজন পিয়নও ফাইল আটকে রেখে সিনিয়র কর্মকর্তার চেয়েও প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে।
পাসপোর্টে নাম সংশোধনের জন্য আদালতের হলফনামা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও, হাবিবুর সাহেব দেখলেন, এই নিয়মগুলো আসলে প্রচ্ছদ মাত্র। দালালদের মাধ্যমে তিনি জানলেন, নাম সংশোধনের জন্য ঘুষ লাগে ৩০-৩২ হাজার টাকা, আর জন্ম তারিখ বদলাতে হলে ৫০ হাজার পর্যন্ত। এই দাম কেবল একটি লেনদেনের নয়; এটি হলো তথাকথিত ‘স্বর্গের টিকিট’, যা নাগরিককে তার অধিকার ফিরে পেতে বাধ্য করে। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা গেছে, প্রতি মাসে শুধু রোহিঙ্গা ও ভারতীয় নাগরিকদের পাসপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে এই সিন্ডিকেট ১০-১৫ কোটি টাকার ঘুষ বাণিজ্য করে। এটি প্রমাণ করে, প্রক্রিয়াটি কতটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।
বরগুনা অফিসের সহকারী পরিচালকের উদাহরণটি হাবিবুর সাহেবকে অবাক করল। কর্মকর্তা নিয়মিত আসেন না। এক সেবাপ্রার্থী জানতে চাইলে তিনি অসুস্থতার কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবে এটি এক পরিকল্পিত কৌশল—কৃত্রিম জট তৈরি করে নাগরিককে দালালের কাছে ঠেলে দেওয়া হয়। দালালই অসুস্থ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে ফাইল পার করে দেয়। যখন পুরো অফিস সম্মিলিতভাবে অপরাধে অংশ নেয়, তখন আর এককভাবে কাউকে দায়ী করা যায় না। এই সম্মিলিত অপরাধবোধ এক ধরনের আত্মরক্ষার বর্ম তৈরি করে, যেখানে প্রত্যেকেই একে অপরের অপকর্মের নীরব সহযোগী। এই ব্যবস্থার কারণে সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি, ১৯৭৯-এর কোনো ধারা কার্যকর থাকে না, কারণ পুরো সিস্টেমই এই অনৈতিক লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল।
হাবিবুর সাহেব এরপর জমির নামজারি করতে গেলেন। এখানে ঘুষের সংস্কৃতি আরও পুরনো—প্রায় মধ্যযুগীয় ভূমিদাস প্রথার মতো। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের প্রতিটি স্তরেই ঘুষ আবশ্যক। নির্ধারিত ফি-এর পাঁচ থেকে সাত গুণ বেশি দিতে হয় নামজারির জন্য। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাব-রেজিস্ট্রার দলিল মূল্যের ১% অগ্রিম ছাড়া কোনো দলিল তৈরি করেন না। সেরেস্তা ফি বাবদ দলিলপ্রতি ২,০০০ টাকা, হেবা ঘোষণায় প্রতি শতাংশে ৩০০ টাকা, বিনিময় দলিলে ৫০০ টাকা, আর উচ্চমূল্যের দলিলে ২০-৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়। নকলের জন্য আলাদা ১,৫০০ টাকা। এই টাকা আদায় করেন সহকারী ও পিয়নরা। পিয়ন ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায় করে, না দিলে দলিল রেজিস্ট্রি বন্ধ করে দেয়।
ভূমি মন্ত্রণালয় নামজারি প্রক্রিয়াকে সহজ ও স্বচ্ছ করতে অনলাইনে আবেদন ও কিউআর কোডের ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই ডিজিটাল ব্যবস্থা কার্যহীন, কারণ কাজ আদায় করতে হলে অদৃশ্য মূল্যতালিকাই মানতে হয়। এই ব্যবস্থায় এক ধরনের ‘রেন্ট-সিকিং’ বা সম্পদ-আহরণের প্রবণতা দেখা যায়। ভূমি অফিসের কর্মচারীরা ভূমি জোনিং, রেকর্ড হালনাগাদ ও খাস জমি ব্যবস্থাপনার মতো উৎপাদনশীল কাজগুলোতে মনোযোগ না দিয়ে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। সাধারণ মানুষের অধিকারকে জিম্মি করে ব্যক্তিগত লাভ করাই এখানে মুখ্য বিষয়। নাগরিকরা নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে এক প্রকার ‘ভূমিদাস’ হয়ে তথাকথিত প্রভুদের খুশি করতে বাধ্য হয়।
হাবিবুর সাহেব উপলব্ধি করলেন, ঘুষ কেবল বিআরটিএ, পাসপোর্ট বা ভূমি অফিসে সীমাবদ্ধ নয়; সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি সরকারি দপ্তরে এটি ছড়িয়ে আছে। যেন এক অদৃশ্য মাকড়সার জাল, যেখানে প্রতিটি সুতো অন্য সুতোয়ের সাথে সংযুক্ত। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘুষ লেনদেনে দ্বিতীয় অবস্থানে। এক অধ্যাপক তাঁর মেয়ের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য পুলিশের হাতে নগদ নয়, ডিজিটাল মাধ্যমে টাকা দেন—যা অপরাধের অকাট্য প্রমাণ রেখে যায়। এটি প্রমাণ করে, ঘুষ এখন প্রযুক্তির সাথেও তাল মিলিয়ে চলছে। তবে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ আদালত বা পুলিশের বদলে জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা বা পারিবারিক সালিশের মতো অনানুষ্ঠানিক পথেই ভরসা রাখে—যা বিচার ব্যবস্থার প্রতি গভীর অনাস্থা নির্দেশ করে।
বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বা লোড বাড়ানোও দুর্নীতিমুক্ত নয়। তিতাস গ্যাসের এক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ—প্রধানমন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে ঘুষের বিনিময়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সংযোগ দিয়েছেন। প্রতিটি সংযোগে ৩-৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে, ঘুষ এখন কেবল ছোটখাটো কাজ নয়, বরং বৃহৎ অবকাঠামো ও শিল্পায়নের নেপথ্য চালিকা শক্তি।
সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত একটি শব্দ হলো ‘উপরি রোজগার’। এটি ঘুষের সামাজিক উপাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরাও এর বাইরে নন; পেনশনের টাকা তুলতে গেলেও ঘুষ দিতে হয়। অর্থাৎ, যিনি সারা জীবন রাষ্ট্রকে সেবা দিয়েছেন, তাকেও নিজের প্রাপ্য ‘ক্রয়’ করতে হয় ঘুষের মাধ্যমে। হাবিবুর সাহেব তখন বুঝলেন, দুর্নীতি এখন আর ব্যতিক্রম নয়, বরং একটি নতুন সামাজিক চুক্তি। নাগরিকরা দ্রুত সেবা পেতে স্বেচ্ছায় ঘুষ দেয়, কারণ তারা বুঝেছে—দ্রুত সেবা পেতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে দেখা যায়, প্রায় ৯.৭৬ শতাংশ নাগরিক স্বেচ্ছায় ঘুষ দেন। যারা ঘুষ দেয়, তাদের ৮৯ শতাংশের প্রধান কারণ হলো—ঘুষ না দিলে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায় না।
এই বাস্তবতা হাবিবুর সাহেবকে এক গভীর নৈতিক সংকটে ফেলে দিল। এতদিন যে নীতির প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তা এখন এক অবাস্তব কল্পনা মনে হলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এই ব্যবস্থায় টিকে থাকতে হলে তাকেও স্রোতে গা ভাসাতে হবে। তার ব্যক্তিগত সততা এখন কেবল তার নিজের জন্য এক অপ্রয়োজনীয় বোঝা, যা তাকে প্রতিনিয়ত হয়রানির মুখে ফেলে। এই মানসিক পরিবর্তন যেন সমগ্র সমাজের এক নীরব পরাজয়ের প্রতিচ্ছবি।
সবশেষে, হাবিবুর সাহেব হাতে নিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) ২০২৪ সালের দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) প্রতিবেদন। তিনি টেবিলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই সূচক অনুযায়ী, বাংলাদেশের অবস্থান ২০২৩ সালের ১০ম স্থান থেকে ২০২৪ সালে ১৪তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি সুখবর মনে হলেও, বাস্তবে দুর্নীতির স্কোর ২৪ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ২৩-এ। অর্থাৎ, দেশটিতে দুর্নীতি বেড়েছে। অবস্থানের এই উন্নতি ঘটেছে শুধু অন্যান্য দেশের আরও খারাপ ফলাফলের কারণে। এটি যেন এক প্রতিযোগিতার নির্মম চিত্র—কে কত ভালোভাবে ব্যর্থ হতে পারে।
এই সূচকের দৃশ্যমান কোনো প্রভাব জনগণের জীবনে পড়ে না। কয়েক দিনের জন্য মিডিয়ায় শোরগোল উঠলেও বাস্তবতা হলো—ঘুষ এখন সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিটি দপ্তর নিজস্ব নিয়মে চলে এই অদৃশ্য ব্যবস্থার ছায়ায়। এমনকি কত শতাংশ ঘুষ কোন কাজে দিতে হবে, তারও এক মোটামুটি মানদণ্ড গড়ে উঠেছে। হাবিবুর সাহেব টেবিলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার এত দিনের নীতিবোধ, যা তাকে দালালদের থেকে দূরে রেখেছিল, এখন কেবল এক অর্থহীন স্মৃতি। এই পরিসংখ্যানগুলো যেন এক নির্জন সমাধির মতো, যেখানে তার আদর্শের কঙ্কাল চাপা পড়ে আছে। তিনি বুঝলেন, এই রাষ্ট্রে অদৃশ্য ব্যবস্থাটিই সব, আর দৃশ্যমান আইন-কানুন কেবল অলংকার, যা মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে রাখে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাগজটি টেবিলের ওপর রাখলেন। তার নীতি আর রাষ্ট্রের বাস্তবতার মধ্যে কোনো সেতুবন্ধন নেই।
