প্রকাশিত : ১২:১১
২৯ আগষ্ট ২০২৫
সর্বশেষ আপডেট: ১২:৩০
২৯ আগষ্ট ২০২৫
জুলাইয়ের অগ্নিগর্ভ উপাখ্যান!
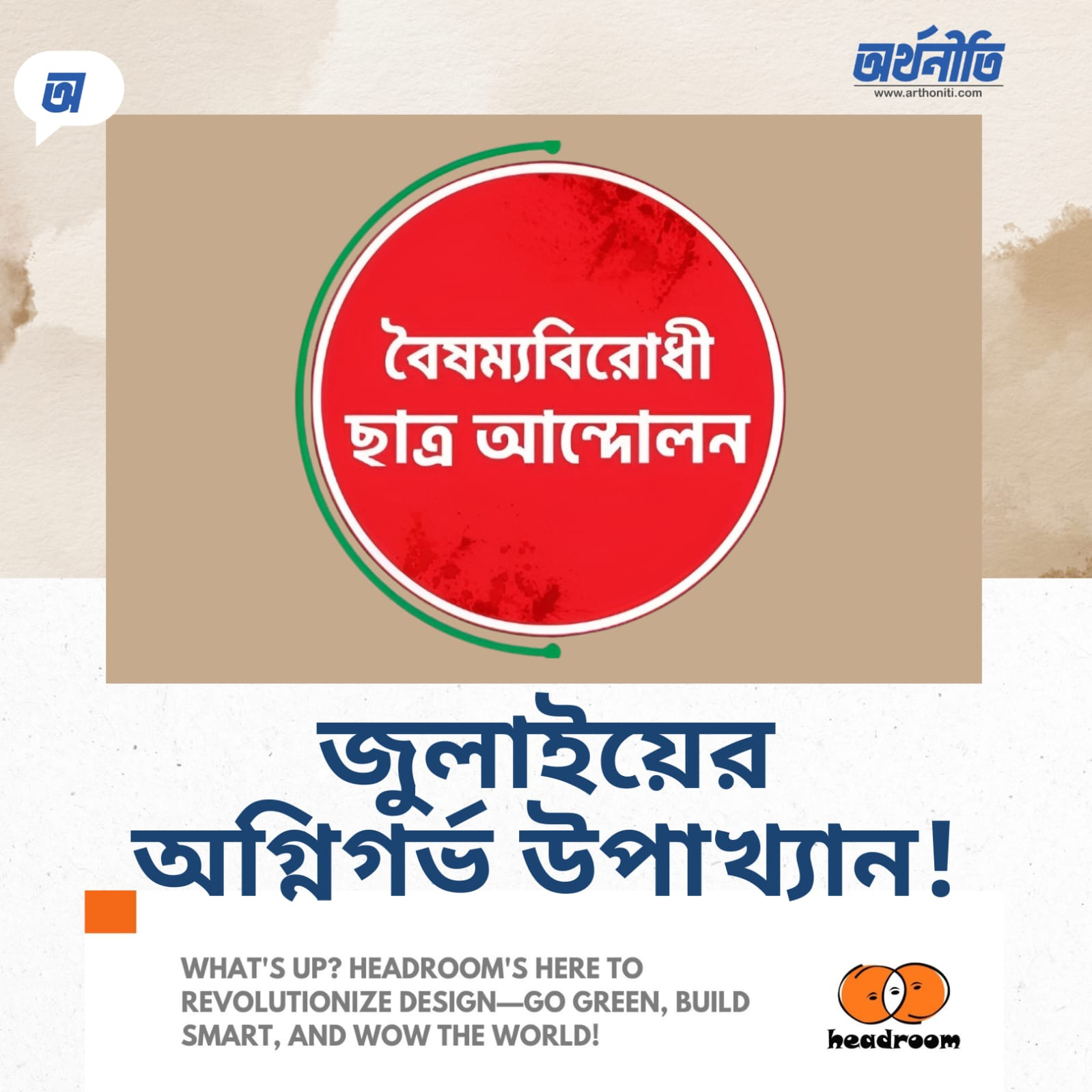
✍️ রেজুয়ান আহম্মেদ
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জুলাই ২০২৪-এর ছাত্র আন্দোলন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি কোটা সংস্কারের একটি নির্দিষ্ট দাবি থেকে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে আমূল পরিবর্তনকারী এক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই আন্দোলন রাতারাতি শুরু হয়নি; এর পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের জমে থাকা গভীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ।
গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও (যেমন পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল নির্মাণ), শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নিপীড়ন, ব্যাপক দুর্নীতি, বিচারহীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার অভিযোগ ক্রমশই বাড়ছিল।
তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং মেধা ও যোগ্যতার পরিবর্তে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে সুযোগ-সুবিধার বিতরণে ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল।
এই চাপা ক্ষোভ একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি ভঙ্গুর ও নিপীড়নমূলক কাঠামোর ইঙ্গিত দিচ্ছিল। একটি নির্দিষ্ট ঘটনা যখন সমাজের এই গভীর ক্ষোভের ওপর স্ফুলিঙ্গের কাজ করে, তখন তা যেকোনো মুহূর্তে গণবিস্ফোরণের কারণ হতে পারে। জুলাই আন্দোলন ছিল সেই স্ফুলিঙ্গেরই বিস্ফোরণ।
এই বিস্ফোরকের সূত্রপাত ঘটে জুন ২০২৪-এর এক উচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে। হাইকোর্ট সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০ শতাংশ পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেয়। এই রায়টি ২০১৮ সালের একটি সার্কুলারকে অবৈধ ঘোষণা করে, যা পূর্ববর্তী কোটাবিরোধী আন্দোলনের পর কোটা পদ্ধতি বাতিল করেছিল। তরুণদের কাছে এই রায়টি শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল না; এটি ছিল মেধার ভিত্তিতে তাদের সীমিত সুযোগের ওপর একটি সরাসরি আঘাত। এটি তাদের মধ্যে বিদ্যমান বঞ্চনা ও অধিকার হারানোর অনুভূতিকে তীব্র করে তোলে, যা দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রাথমিক ইন্ধন জোগায়।
আন্দোলনের প্রথম ধাপ ছিল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই প্রতিবাদের সূচনা করে, যা দ্রুত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। ঈদ ও গ্রীষ্মের ছুটির পর ১ জুলাই থেকে শিক্ষার্থীরা পুনরায় সংগঠিত হয় এবং ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ নামে একটি নতুন সমন্বয়কারী প্ল্যাটফর্ম গঠন করে।
এই প্ল্যাটফর্মের ডাকে শিক্ষার্থীরা ‘বাংলা ব্লকেড’ কর্মসূচি শুরু করে, যার মাধ্যমে তারা শাহবাগসহ রাজধানীর প্রধান সড়ক ও রেললাইন অবরোধ করে পুরো রাজধানীকে অচল করে দেয়। এই কৌশলটি ছিল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের একটি শক্তিশালী রূপ, যা সরকারের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করে।
এই আন্দোলন পূর্ববর্তী বিভিন্ন আন্দোলন থেকে ভিন্ন ছিল, কারণ এর নেতৃত্ব ছিল বিকেন্দ্রীভূত ও স্বতঃস্ফূর্ত।
কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব না থাকায় এটিকে দমন করা সরকারের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, এবং এই দমন-পীড়নই শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকে একটি নির্দিষ্ট দাবি থেকে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করে।
প্রতিরোধের দেয়াল ও রাজাকারের মন্তব্য
আন্দোলনের শুরুতে এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কোটা সংস্কারের দাবি আদায়। তবে ১৬ জুলাইয়ের পর এর গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।
১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-সমর্থিত ছাত্র সংগঠন, ছাত্রলীগের সদস্যদের এবং পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেশব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দেয়। এই সময় থেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে যুক্ত হতে শুরু করে, যা আন্দোলনের তীব্রতাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।
ধীরে ধীরে এই আন্দোলন শুধুমাত্র ছাত্রদের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী, শিল্পী, লেখক, আইনজীবী, প্রবাসী, এমনকি রিকশাচালকরাও এতে যুক্ত হয়, যা এটিকে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আন্দোলন থেকে জাতীয় চেতনার আন্দোলনে পরিণত করে।
আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে ১৪ জুলাই।
সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেন:
"মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা সুবিধা পাবে না? তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা পাবে?" বাংলাদেশের ইতিহাসে ‘রাজাকার’ শব্দটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করা বিশ্বাসঘাতকদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি চরম ঘৃণার প্রতীক।
এই মন্তব্যের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন, যা ছাত্রদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়।
এর প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ফুঁসে ওঠে এবং ‘তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার’ ও ‘চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার’-এর মতো স্লোগান দিতে শুরু করে।
এই মন্তব্যটি আন্দোলনকে একটি নৈতিক আঘাত (moral shock) দেয়। এটি আন্দোলনকে কেবল কোটা সংস্কারের একটি প্রশাসনিক দাবি থেকে সরকারের নৈতিক বৈধতা ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপকতর সংগ্রামে রূপান্তরিত করে।
ছাত্ররা এই অপমানকে তাদের প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই স্লোগানগুলো আন্দোলনের নতুন প্রাণশক্তি ও রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ঘটনার পর সরকার-সমর্থিত গোষ্ঠী, বিশেষ করে ছাত্রলীগের সদস্যরা, আন্দোলনকারীদের ওপর সশস্ত্র হামলা শুরু করে।
তারা লাঠি, ধারালো অস্ত্র, এমনকি আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল থেকে বের করে দেয় এবং হলগুলোতে তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে।
রক্তাক্ত জুলাই: শহীদের নামে প্রতিরোধের মন্ত্র
আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমন-পীড়ন আরও হিংস্র রূপ ধারণ করে, যা এক ভয়াবহ গণহত্যার জন্ম দেয়। এই গণহত্যায় হতাহতের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার তথ্যে ব্যাপক অমিল পরিলক্ষিত হয়, যা তৎকালীন সরকারের তথ্য গোপনের প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।
বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হতাহতের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:
সরকারি রিপোর্ট (২ আগস্ট পর্যন্ত): নিহত: ২১৫ জন,
জাতিসংঘের রিপোর্ট (১২ ,
ফেব্রুয়ারি, ২০২৫): নিহত: ১,৪০০+ (১২-১৩% শিশু),
মানবাধিকার সংস্থা ও গণমাধ্যম: নিহত: ১,০০০+
এই পরিসংখ্যানগুলো শুধুমাত্র সংখ্যা নয়, বরং প্রতিটি সংখ্যা একটি পরিবারের ট্র্যাজেডি, যা আন্দোলনকে আরও বেশি মানবিক ও রাজনৈতিক করে তোলে। হাসপাতাল থেকে সিসিটিভি ফুটেজ জব্দ করা, অপ্রকাশিত লাশ দাফন করা এবং আহতদের চিকিৎসাসেবা প্রদানে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনাগুলো সরকারের বর্বরতার প্রমাণ দেয়।
১৬ জুলাই রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের শাহাদাত আন্দোলনকে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। পুলিশের সামনে দু’হাত প্রসারিত করে বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকা তার ছবিটি প্রতিরোধের এক শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত হয়।
সাঈদের মৃত্যু কোটা সংস্কারের আন্দোলনকে ন্যায়বিচারের এক সংগ্রামে পরিণত করে। তার মা'র প্রশ্ন, "আমার ছেলেকে কেন খুন করা হলো?" আন্দোলনের একটি মানবিক আবেদন তৈরি করে এবং সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে। সাঈদের মৃত্যু প্রমাণ করে যে দমন-পীড়ন আন্দোলনকে স্তিমিত করার পরিবর্তে আরও শক্তিশালী করে তোলে।
আরেকটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ১৮ জুলাই ঘটে, যখন ফ্রিল্যান্সার মীর মুগ্ধ আন্দোলনকারীদের জন্য পানি ও বিস্কুট বিতরণকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। মৃত্যুর কিছু মুহূর্ত আগে ধারণ করা একটি ভাইরাল ভিডিওতে তাকে ‘পানি লাগবে, পানি’ বলতে শোনা যায়।
মুগ্ধর এই আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে আন্দোলনটি কেবল অধিকার আদায়ের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল সহমর্মিতা ও মানবতাবোধের এক অনন্য প্রকাশ। ‘পানি লাগবে, পানি’ স্লোগানটি একটি সাধারণ মানবিক আবেদন থেকে সংহতি ও সংকল্পের প্রতীকে পরিণত হয়। তার গল্পটি আন্দোলনের মানবিক দিককে তুলে ধরে এবং দেখায় যে আন্দোলনকারীরা শুধুমাত্র নিজেদের অধিকারের জন্য লড়েনি, বরং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সংহতির এক নতুন মডেল তৈরি করেছিল।
এই গণহত্যার শিকার অনেকেই শারীরিক ও মানসিক ট্রমার শিকার হন।
১৯ বছর বয়সী শোয়াইকতের মতো অনেক তরুণ তাদের পরিবারের বারণ সত্ত্বেও আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রাণ হারান। তাদের পরিবারের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, কীভাবে একটি মধ্যবিত্ত পরিবার এই ঘটনায় ভেঙে পড়ে এবং ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করে। অনেক পরিবার তাদের সব সঞ্চয় আহত সদস্যদের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করে, যা তাদের নতুন করে অর্থনৈতিক সংকটে ফেলে।
বিপ্লবের রঙ, সুর ও শব্দ: শিল্প ও সংস্কৃতির ভূমিকা
জুলাই আন্দোলনের সময় ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্প ও সংস্কৃতি প্রতিরোধের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়।
প্রতিবাদী গান, হিপ-হপ, দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি আন্দোলনকারীদের মনোবল দৃঢ় করতে এবং দেশব্যাপী গণমানুষের মধ্যে সংহতি তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
হিপ-হপ শিল্পী Shezan-এর ‘কথা ক’ এবং Hannan-এর ‘আওয়াজ উঠা’-র মতো গানগুলো দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। Mousumi-এর গান ‘দেশটা তোমার বাপের নাকি?’ সরাসরি সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে আঘাত হানে। এই গানগুলো ইন্টারনেট বন্ধ থাকলেও মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।
হিপ-হপ সংস্কৃতির উত্থান একটি নতুন প্রজন্মের প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সামনে আসে। এটি একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন, যেখানে তরুণ শিল্পীরা সরাসরি রাজনৈতিক বার্তা দিতে দ্বিধা করেনি। Hannan-কে গ্রেফতার করা হয়, যা প্রমাণ করে যে সরকার এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের শক্তিকে ভয় পেয়েছিল।
ঢাকা ও অন্যান্য শহরের দেয়ালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখা গ্রাফিতিগুলো প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। ‘জুলাই ৩৬’, ‘আয়নাঘর’, ‘আমার ছেলেকে কেন খুন করা হলো?’, এবং ‘আমরা দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছি’-এর মতো দেয়াল লিখনগুলো আন্দোলনের মূল বার্তা বহন করে। গ্রাফিতিগুলো ছিল একটি বিকেন্দ্রীভূত ও বেনামী মাধ্যম, যা দমন করা সহজ ছিল না। এটি মানুষের হৃদয়ে সঞ্চিত ক্ষোভের এক দৃশ্যমান প্রকাশ ছিল এবং প্রমাণ করে যে যখন বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়, তখন প্রতিরোধ তার ভিন্ন রূপ ধারণ করে।
এই আন্দোলন ছিল একটি নতুন ডিজিটাল প্রজন্মের আন্দোলন। সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দিলেও, ভিপিএন এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সহায়তায় খবর ছড়িয়ে পড়ে।
সামাজিক মাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক ও টেলিগ্রাম, যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। ব্যক্তিগত গল্প, ছবি ও ভিডিও (যেমন আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধর ভিডিও) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা আন্দোলনকে আরও বেগবান করে এবং আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করে।
এক নতুন ভোরের সন্ধানে: পতনের পর
জুলাইয়ের শেষের দিকে আন্দোলনকারীরা এক দফা দাবিতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। তারা ট্যাক্স ও বিল না দেওয়া, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা বন্ধ রাখার মতো কর্মসূচি গ্রহণ করে।
এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৪ আগস্ট সারাদেশ অচল হয়ে যায়। ব্যাপক জনরোষের মুখে শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে দেশত্যাগ করেন। এই পতনে সামরিক বাহিনীর নিরপেক্ষ অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতীতে সামরিক বাহিনী সরাসরি ক্ষমতা দখল করেছে, কিন্তু এবার তারা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে তাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানের কারণে সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে বিরত ছিল। এই নিরপেক্ষতা আন্দোলনকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়।
৫ আগস্ট সরকারের পতনের পর, ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। ছাত্র আন্দোলনের দুইজন সমন্বয়ক, নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ, উপদেষ্টা হিসেবে সরকারে যোগ দেন।
ছাত্র আন্দোলন সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা না চাইলেও, তাদের নেতৃত্ব থেকে উঠে আসা ব্যক্তিরা সরকারে স্থান পান, যা ইঙ্গিত দেয় যে ছাত্ররা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে না থেকেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব ফেলছে।
তবে নতুন সরকারের সামনে ছিল বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। শেখ হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়া ১৮ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা একটি বড় সংকট ছিল। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করাও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।
রাজনৈতিকভাবে, নির্বাচন, রাষ্ট্র সংস্কার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP) গঠন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।
বিজয় বঞ্চনা ও সামাজিক অস্থিরতা
আন্দোলনের সাফল্যের পরেও বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং গভীর সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়।
‘মব জাস্টিস’ বা গণপিটুনি ও পরিকল্পিত হত্যার ঘটনা বেড়ে যায়, এবং অন্তত ৪২ জন পুলিশ সদস্য জনতার হামলায় নিহত হন। এই ধরনের সহিংসতা দীর্ঘদিনের দমন-পীড়ন ও বিচারহীনতার ক্ষোভ থেকেই সৃষ্টি হয়। একটি রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যখন জনগণের আস্থা হারায়, তখন সমাজ তার নিজস্ব অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো হারিয়ে ফেলে।
৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর হিন্দু ও আহমদিয়া মুসলিমদের ওপর ব্যাপক হামলা, মন্দির ও বাড়িঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এই হামলাগুলো ছিল মূলত সাবেক সরকারের সমর্থক হিসেবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা, স্থানীয় বিরোধ বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ।
এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, একটি ফ্যাসিবাদী সরকার পতনের পর সৃষ্ট শূন্যতা ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠী ও স্বার্থান্বেষী মহল দ্বারা পূরণ হতে পারে।
এই আন্দোলনে গার্মেন্টস শ্রমিক ও রিকশাচালকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। একজন রিকশাচালক ইসমাইলের মৃত্যুও আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল।
কিন্তু সরকার পতনের পর অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায়, যা হাজার হাজার শ্রমিককে, যাদের অধিকাংশই নারী, বেকার করে ফেলে। তাদের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও তাদের অর্থনৈতিক সংকট কাটেনি, যা বিপ্লবের সুফল থেকে তাদের বঞ্চনার ইঙ্গিত দেয়।
অসমাপ্ত বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি
জুলাই বিপ্লব ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে ‘৫২-এর ভাষা আন্দোলন’, ‘৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান’ এবং ‘৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ’-এর মতোই একটি ছাত্র-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন, যা জনগণের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র সমাজই পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি। এই আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তরুণী শিক্ষার্থীরা মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছে, মানব ঢাল তৈরি করেছে এবং আহতদের সেবা করেছে। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া এই আন্দোলন সফল হতো না বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই আন্দোলনের এক গভীর সীমাবদ্ধতা উন্মোচিত হয় যখন দেখা যায়, সম্মুখভাগে নেতৃত্ব দেওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই।
এটি বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক গভীর সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসে, যেখানে নারীদের ত্যাগ ও অবদান প্রায়শই উপেক্ষিত হয়।
এই আন্দোলন একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হলেও, বিপ্লব-পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা নতুন করে হতাশার জন্ম দিয়েছে।
ড. ইউনূস সরকারের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলো জটিল এবং বহুমুখী।
ড. ইউনূস সরকারের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ:
সাবেক সরকারের রেখে যাওয়া বিপুল ঋণ, মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার সংকট।
ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।
দ্রুততম সময়ে নির্বাচন, রাষ্ট্র সংস্কার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও ‘মব জাস্টিস’ নিয়ন্ত্রণ।
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
এই বিপ্লব সফল হলেও এটি ছিল একটি অসমাপ্ত বিপ্লব।
এটি একটি নতুন প্রজন্মের সামনে স্বপ্ন ও বাস্তবতার এক কঠিন লড়াই তুলে ধরেছে।
ড. ইউনূস সরকারের সামনে রয়েছে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, দুর্নীতি দমন, এবং একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কঠিন পথ।
