প্রকাশিত : ০৫:৫৪
১০ আগষ্ট ২০২৫
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন: আস্থা পুনর্গঠনের সাফল্য–ব্যর্থতার মোড়!
সম্পাদকীয় কলাম
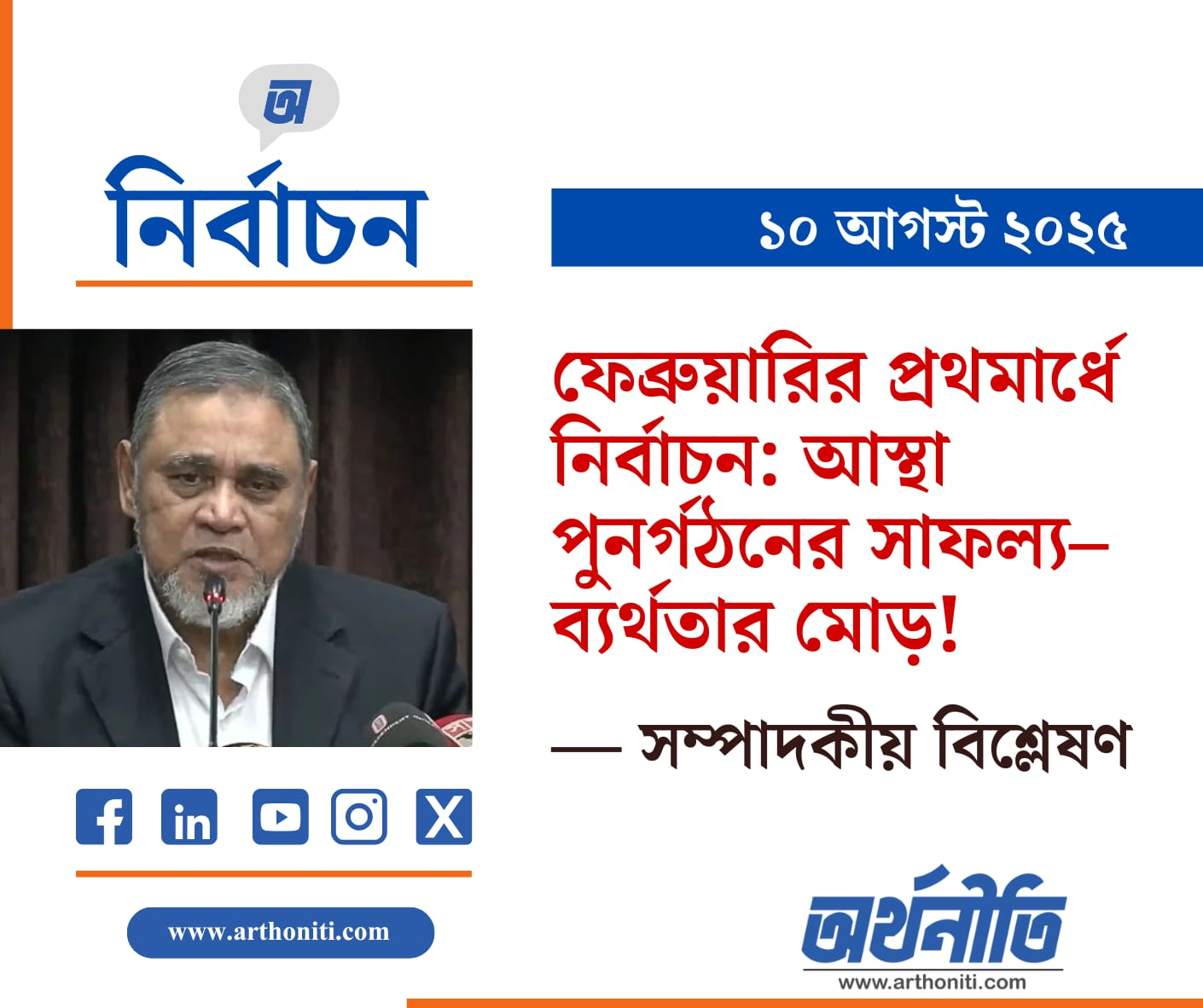
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে—প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের এই ঘোষণা শুধু নির্বাচনের সময়সীমা জানানো নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলের ইঙ্গিত। রংপুরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে তিনি যে বার্তা দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট—আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের সামনে যেমন বড় সুযোগ রয়েছে, তেমনি রয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জও।
সিইসি নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন যে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী প্রশাসন এবং সমগ্র ভোট প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের অভিযোগ—প্রশাসনিক পক্ষপাত, প্রার্থীদের সমান সুযোগের অভাব এবং নির্বাচনী সহিংসতা। অনেকে মনে করেন, বিগত কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের অভাব ভোটারদের ভোটকেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ভোটের হার কমেছে, ভোটারদের আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে, আর নির্বাচনী প্রক্রিয়া অনেকের কাছে গুরুত্ব হারিয়েছে।
সিইসি’র মন্তব্য—“মানুষ ভোটকেন্দ্রে যাওয়া ভুলে গেছে”—শুধু হতাশার বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এটি একটি সামাজিক–রাজনৈতিক বাস্তবতা। মানুষ ভোট দিতে গেলে তাদের মতামত প্রতিফলিত হবে—এই বিশ্বাসটাই হারিয়ে ফেলেছে। সেই হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনা হবে আসন্ন নির্বাচনের প্রধান শর্ত।
আগে নির্বাচনের সময় বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অস্ত্র, সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। কিন্তু সিইসি এবার একেবারে নতুন এক হুমকির কথা বলেছেন—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির অপব্যবহার। এআই এখন তথ্য বিকৃতি, ভুয়া ভিডিও বা ছবি তৈরি এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের সময়ে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুজব, চরিত্রহনন বা ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া ভোটারদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে, এমনকি সহিংসতা উসকে দিতে পারে।
বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রসার যত দ্রুত ঘটেছে, তত দ্রুতই বেড়েছে এর অপব্যবহার। সিইসি স্পষ্ট করে বলেছেন, পেশাদার সাংবাদিকদের তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেন না; কিন্তু যারা ফেসবুকভিত্তিক ‘সাংবাদিকতা’ করেন, কোনো প্রশিক্ষণ বা দায়বদ্ধতা ছাড়াই কনটেন্ট তৈরি করেন, তারাই বিভ্রান্তির বড় উৎস হতে পারেন। বিশেষ করে যখন এই কনটেন্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়ে তৈরি হয় এবং যাচাই-বাছাই ছাড়াই হাজারো মানুষ তা শেয়ার করে, তখন তা জনমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে।
গণমাধ্যম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সিইসি পেশাদার সাংবাদিকদের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন, তারা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করবেন। তবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করাও সমানভাবে জরুরি। সাংবাদিকরা যদি তথ্য উপস্থাপনে নিরপেক্ষ না থাকেন, তাহলে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
এখানে নির্বাচন কমিশনেরও করণীয় রয়েছে—তথ্য প্রবাহ স্বচ্ছ রাখা, সাংবাদিকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সহজলভ্য করা এবং মিডিয়ার প্রশ্নের উত্তর দ্রুত ও সৎভাবে প্রদান করা।
সিইসি বলেছেন, বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো এবং তা আরও উন্নতির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, নির্বাচনের সময় মাঠপর্যায়ে অনেক অনিয়ম ও সহিংসতা ঘটতে পারে—বিশেষত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, ভোটকেন্দ্র দখল কিংবা প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার। এজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।
মাঠ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যদি সব প্রার্থীকে সমান নিরাপত্তা দিতে পারে, ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে এবং ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে পারে, তবেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে।
বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়—এটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উন্নয়ন সহযোগী দেশ, বাণিজ্যিক অংশীদার এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচন কতটা স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। নির্বাচনের মান যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তবে তা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
কোনো নির্বাচন কেবল নির্বাচন কমিশনের ওপর নির্ভরশীল নয়—রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে দলগুলোকে সহনশীলতা, সংলাপ ও আপসের পথে আসতে হবে। যদি রাজনৈতিক দলগুলো সহিংসতা ও উসকানির পথে চলে, তবে নির্বাচন কমিশনের প্রচেষ্টা অনেকাংশেই ব্যর্থ হবে।
সিইসি যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন, সেটি আসলেই বাস্তব। এজন্য প্রয়োজন সচেতনতামূলক কার্যক্রম—গ্রাম থেকে শহর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মক্ষেত্র—সবখানেই ভোটের গুরুত্ব বোঝানো। ভোট দেওয়া যে শুধু অধিকার নয়, বরং দায়িত্ব—এটি নাগরিকদের মনে করিয়ে দিতে হবে।
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্ধারিত ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য হতে পারে গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণের সূচনা। কিন্তু এই সূচনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে; আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে হতে হবে পেশাদার; গণমাধ্যমকে হতে হবে নিরপেক্ষ ও তথ্যনিষ্ঠ; আর রাজনৈতিক দলগুলোকে ত্যাগ করতে হবে সহিংসতা ও অনমনীয়তা।
নির্বাচন শুধু একটি দিনের ঘটনা নয়—এটি একটি পূর্ণ প্রক্রিয়া, যা শুরু হয় প্রস্তুতি থেকে এবং শেষ হয় জনআস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে। সব পক্ষ যদি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে, তাহলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হতে পারে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়; আর যদি ব্যর্থ হয়, তবে তা আরও গভীর করবে আস্থাহীনতার সংকট।
